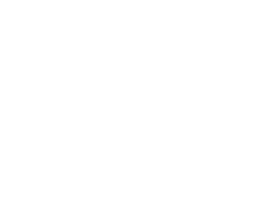এটা এমন নয় যে, এ-ধরনের বিষয় ঐকান্তিকতার বিরোধিতা করে বসে—যদিও এই ঐকান্তিকতাকে খানিকটা হাস্যকর মনে হতো, যেখানে একমাত্র মিথ্যাকে একান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। বিষয়টা এমন যে, পৃথিবীর বস্তুনির্ভর বাস্তবতা আমাদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ দার্শনিক সত্য, যেখানে আমি ১৯৫৫ সালে শরতের চমৎকার একদিনে হঠাৎ করে উপলব্ধি করলাম—পৃথিবীতে একমাত্র যে বাস্তবতা বিদ্যমান সেটা হল আমি; আমার নিজের জীবন।
আমি সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির কথা বলছি। যদি বিশ্বটা হয় একটি বস্তুনির্ভর বাস্তবতা, যা আমাদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান, তাহলে মানুষ নিজেরাই এমনকি নিজেদের চোখে, বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়; এবং তাদের জীবনের কেচ্ছা ইতিহাসের কিছু বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা মাত্র—যেটাতে তারা বিস্মিত হতে পারে, তবে তাতে তাদের কিছুই করার নেই। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সজ্জিতভাবে সন্নিবেশনের কোনো অর্থ দাঁড়ায় না।
এক বছর পরে, ১৯৫৬ সালে, হাঙ্গেরির বিপ্লব শুরু হলো। ক্ষণিক সময়ের ভেতরেই দেশটি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো। যদিও সোভিয়েত ট্যাংকগুলো আরো আগেই বস্তুনির্ভরতা পুনঃস্থাপিত করেছিল। আমি বিষয়টা নিয়ে কোনো ঠাট্টা করছি না। বিংশ শতকে ভাষার কি হয়েছিল ভেবে দেখুন, শব্দের কি হয়েছিল! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের সময়ের লেখকদের সবচেয়ে প্রথম ও ভীতিকর আবিষ্কার ছিল ঐ ভাষা, যেটা যে ফর্মে আমাদের কাছে এসেছিল, একটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আদিকালিক সংস্কৃতি হিসেবে, সেটা আমাদের চেতনা ও বাস্তবতাকে ধারণ করার উপযুক্ত ছিল না। কাফকার কথা ভাবুন, অরওয়েলের কথা ভাবুন, যাদের হাতে পুরানো ভাষা খণ্ডিত হয়ে গেছে। যেন তারা ঐটাকে বারবার জ্বলন্ত আগুনে ছুড়ে দিয়েছিল, সবশেষ ঐ ছাইটুকু দেখার জন্য, ঐভাবে নতুন ও পূর্বে অজানা কতক কাঠামোর জন্ম হয়েছিল।
তবে আমি এখন আমার সবচেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়—আমার লেখালেখি প্রসঙ্গে কথা বলবো। জা পল সাঁর্তে তার একটি ছোট বইয়ের সমস্তটা জুড়ে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন—আমরা কার জন্য লিখি? এটা বেশ মজার প্রশ্ন, তবে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই এজন্যে যে, এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়নি। দেখা যাক বিপদটা আসলে কোথায়। যদি একজন লেখককে তার পছন্দসই কোনো সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠীকে বেছে নিতে হয়—শুধুমাত্র আনন্দদানে নয়, প্রভাবিত করার জন্যেও। তবে শুরুতে তার লেখার ধরণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, এটা প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা রাখে কিনা। তিনি খুব শীঘ্রই সংশয়ের আঘাতে জর্জরিত হবেন; এবং নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকবেন। তিনি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে, তার পাঠকরা আসলে কি চায়—তারা কি পছন্দ করে? তিনি নিশ্চয় সকলকে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। যদি তিনি তা করেনও, তাও কোনো কাজে আসবে না। তাকে তার ভেতরে সম্ভাব্য পাঠকদের যে চিত্র আছে, তার ওপর নির্ভর করতে হবে—যে প্রত্যাশা তিনি তাদের কাছে করেন। তাহলে একজন লেখক কার জন্য লেখেন? উত্তরটা পরিষ্কার: তিনি নিজের জন্য লেখেন।
অন্তত আমি এ কথা হলফ করে বলতে পারি। আমি খুব সোজাসাফটা এই উত্তরে পৌঁছেছি। আমার জন্য এটা সহজই ছিল, আমার কোনো পাঠক ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ছিল না কাউকে প্রভাবান্বিত করার। আমি কোনো বিশেষ কারণে লেখালেখি করিনি। আমি যা লিখেছি কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। যদি আমার তেমন কোনো লক্ষ থাকতো—সেটা হতো বিশ্বস্ত থাকা, ভাষা এবং গঠনরীতির ওপর। আর বিষয়বস্তুর ওপর। এর বেশি কিছু না। এটা পরিষ্কার করার খুব দরকার ছিল ঐ উপহাসতুল্য এবং বিষাদময় সময়ে যখন সাহিত্য ছিল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও কর্তব্যরত।
অন্য একটা প্রশ্ন আছে, যদিও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত তথাপি সন্দেহপূর্ণ; এটার উত্তর দেওয়া আরো শক্ত: আমরা কেন লিখি? এক্ষেত্রেও আমি বেশ ভাগ্যবান যে আমাকে কখনো এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমি আমার উপন্যাস ‘ফেইলর’-এ একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছি। আমি একটি অফিস ভবনের খালি করিডরে দাঁড়িয়েছিলাম। আড়াআড়িভাবে ছেদ করে যাওয়া অপর করিডর থেকে আমি একটা পদধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আমাকে ধরে রেখেছিল। শব্দটা বেড়েই চলছিল। যদিও সেটা ছিল একটা অদৃশ্য মানুষের পদধ্বনি। আমার কাছে মনে হলো, আমি যেন কয়েকহাজার মানুষের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। যেন এক বিশাল মিছিল এই করিডর দিয়ে ধেয়ে আসছে। ঐ সময় আমার ইন্দ্রিয়গোচর হলো ঐ পদধ্বনির দিকে আমার অদম্য আকর্ষণ, যেটা আবার প্রতি মুহূর্তে দ্বিগুণ হচ্ছিল। ক্ষণিক সময়ের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম, আত্ম-উদ্দামতার পরমানন্দ, জনস্রোতের ভেতর মিশে যাওয়ার উন্মাতাল আনন্দ—নিটসে যাকে বলছেন, যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গে, তবে সেটা এখানেও প্রাসঙ্গিক—একধরনের ডাইনোসিয়ান অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছিল কোনো শারীরিক শক্তি আমাকে ঠেলে পাঠাচ্ছিল, টেনে ধরছিল ঐ অদেখা মিছিলের দিকে। আমি অনুভব করলাম, আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এই অদম্য-আকর্ষণীয় শক্তি থেকে বাঁচতে হলে, দেয়ালের বিপরীতে ধাক্কা দিতে হবে।
প্রতিটা লেখক এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। একসময় এটাকে বলা হতো ক্ষণিক অনুপ্রেরণা। এরপরও আমি এই অভিজ্ঞতাকে শৈল্পিক উদ্ঘাটনের পর্যায়ে কল্পনা করবো না। বরং আমি এটাকে অস্তিত্ববাদী আত্ম-আবিষ্কারের ভেতর আনবো। আমি এটার ভেতর দিয়ে যা পেয়েছি, সেটা আমার শিল্পবোধ নয়—এটার কলকব্জা কিছু সময়ের জন্য আমার হাতে ছিল না—তবে আমি জীবন পেয়েছি, যা হারাতে বসেছিলাম। অভিজ্ঞতাটি ছিল নিঃসঙ্গতাকেন্দ্রিক আরো কঠিন জীবন। আমার ভয়ের জায়গাটা হলো, নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ফিরে আসার দশ বছর পর আমি উপলব্ধি করেছিলাম, সমস্ত অভিজ্ঞতার কিছু বিহ্বল অভিব্যক্তি, খণ্ড খণ্ড স্মৃতি, যেন এটা আমার সঙ্গে ঘটেনি।
আমি একবার বলেছিলাম যে, তথাকথিত সমাজতন্ত্র আমার কাছে সামান্য ছোট আকারের মুখরোচক কেকের মতো, যেটা প্রুস্তের চায়ের মধ্যে মিশে তার ভেতর ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের গন্ধটা জাগিয়ে তোলে। যে ভাষায় আমি কথা বলি তা নিয়ে কিছু করার জন্য ১৯৫৬ সালের বিদ্রোহ দমন হওয়ার পর হাঙ্গেরিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ঐভাবে আমি প্রত্যক্ষ করতে শিখলাম কিভাবে একনায়কতন্ত্র কাজ করে। আমি দেখলাম কিভাবে পুরো জাতিকে তার আদর্শগুলোকে অস্বীকার করতে শেখানো হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম, আশা জাগিয়ে রাখা হলো শয়তানের প্রধান অস্ত্র।
কেউ কি একজন লেখকের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করার কথা ভাবতে পারেন—এমনকি ক্ষয়িঞ্চু একনায়কতন্ত্রের ভেতর? ১৯৬০ সালের দিকে হাঙ্গেরির একনায়কতন্ত্র সংহতকরণের এমন একপর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, তাকে আর একটু হলেই বলা যেত সামাজিক ঐকমত্য। পশ্চিম পরে সেটা অনুকরণ করলো, নাম দিলো গাওলাশ কম্যুনিজম।
একজন লেখককে তার খরচ চালিয়ে নেয়ার জন্য খুব বেশি লাগে না। তার শুধু দরকার হয় খাতা আর কলম। বিতৃষ্ণাবোধ আর বিষাদগ্রস্ততা, যেটা নিয়ে আমি প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠি, তৎক্ষণাৎ আমি যে পৃথিবীর কথা বলতে চাই, সেখানে নিয়ে যায়। আমাকে আবিষ্কার করতে হয় যে, আমি একধরনের সমগ্রতাবাদের যুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠা এক ব্যক্তিকে অন্য এক সমগ্রতাবাদে নিক্ষেপ করছি। এই কারণে আমার উপন্যাসের ভাষা হয়ে উঠেছে অতি মাত্রায় পরোক্ষ উল্লেখসংবলিত মাধ্যম। যদি আমি এখন পেছন ফিরে তাকাই, এবং ঐ সময় আমি যে পরিস্থিতিতে ছিলাম সেটা সম্পর্কে ধারণা পেতে চেষ্টা করি—আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, পশ্চিমে একান্ত মুক্ত সমাজে থাকলে আমি খুব সম্ভবত আপনাদের অতি পরিচিত ‘ফেইটলেস’ উপন্যাসটি লিখতে সক্ষম হতাম না।
খুব সম্ভবত আমি অন্যকিছু করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতাম। তার মানে এই নয় যে, আমি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে চেষ্টা করতাম না। হয়ত অন্য একটা সত্যের পিছনে ছুটতাম। বই এবং চিন্তাজগতের মুক্তবাজার সংস্কৃতিতে আমিও দেখানোর মতো উপন্যাস লিখতে চাইতাম—উদাহরণস্বরূপ, আমি হয়ত আমার উপন্যাসে সময়কে ভেঙে-চুরে ফেলতাম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দৃশ্যগুলোর বর্ণনা দিতাম। কিন্তু আমার উপন্যাসের নায়ক তার সময়ের সেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বাস করে না। তার সময় ও ভাষাটা আলাদা। এমনকি, সেই ব্যক্তিও আর সেই ব্যক্তি নেই। সে আর কিছুই মনে করতে পারে না। তবে সে বেঁচে থাকে। কাজেই তাকে নিস্তেজ হয়ে যেতে হয়—সরলরৈখিক জীবনের বিষণ্ণ গোলকধাঁধায়। সে যন্ত্রণাদায়ক ঐ স্মৃতিগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। চমৎকার কিছু চরম ও বিষণ্ণ মুহূর্তের চেয়ে তাকে বাস করতে হয় সবধরনের নিপীড়ন এবং একঘেয়েমিতার মধ্যে।
কাজেই আমি অগ্রসর হয়েছিলাম ধাপে ধাপে আবিষ্কারের সরলরৈখিক পথে। এটা ছিল আমার আবিষ্কারের বিদ্যা। আমি যথাশীঘ্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমি কার জন্য লিখছি এবং কেন লিখছি, এই বিষয়ে আদৌ আগ্রহী ছিলাম না। একটা বিষয় খালি আমাকে টানতো, সাহিত্যের সঙ্গে বা সাহিত্য নিয়ে আমার কি করার আছে? কেননা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে, একটা অনতিক্রম্য সীমারেখা সাহিত্য ও চিন্তাধারা থেকে আমাকে আলাদা রেখেছে; আলাদা করে রেখেছে সাহিত্যের আপন সত্তা থেকেও। এই সীমানানির্ধারক সীমারেখার নাম, অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই, ‘আউশহ্বিটজ’।
আমার লেখায় ঐ ধ্বংসযজ্ঞ কখনও অতীতকালের ক্রিয়ায় বর্তমান থাকতে পারতো না। আমার সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়—কেউ এটাকে প্রশংসা হিসেবে নেয়, কেউ অভিযোগ—আমি কেবল একটা বিষয়েই লিখি, সেটা হলো ধ্বংসযজ্ঞ। তাদের সঙ্গে আমার কোনোই বিরোধ নেই। আমাকে লাইব্রেরির তাকে কোনো একটি বিশেষ অভিধায় আখ্যায়িত করে রাখলে আমার আপত্তি থাকবে কেন? আজকের কোন লেখক ধ্বংসযজ্ঞের লেখক নন? যে ভাঙাস্বর আধুনিক ইউরোপিয়ান শিল্পকে কয়েকদশক ধরে দমিয়ে রেখেছে তাকে চিহ্নিত করার জন্য কাউকে আর বিষয়বস্তু হিসেবে ধ্বংসযজ্ঞকে বেছে নিতে হবে না। একটু বাড়িয়ে বলছি মনে হলেও বলছি, আমি এমন কোনো প্রকৃত বা খাঁটি শিল্পের কথা জানি না, যেখানে এই ভাঙনটার প্রতিফলন ঘটেনি।