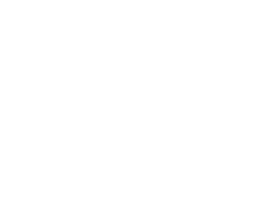যে গল্প তাড়িয়ে বেড়ায় সেটি নিয়ে ছবি বানাই
কলেজজীবনে নাটকের দল গড়েছেন, পরে চলচ্চিত্র আন্দোলনেও জড়িয়েছেন। ‘আগামী’ ও ‘চাকা’র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম। বানিয়েছেন ‘দীপু নাম্বার টু’, ‘আমার বন্ধু রাশেদ’সহ বেশ কটি ছবি। তাঁর সিনেমাজীবনের মুখোমুখি হয়েছেন ওমর শাহেদ। ছবি তুলেছেন কাকলী প্রধান
লিটল থিয়েটার কবে করলেন?
আগেও নাটকের দল করেছি। আমাদের ‘শিশুনাট্যম’-এর প্রধান ছিলেন উদয়ন স্কুলের অধ্যক্ষ বেগম মমতাজ হোসেন। মাঝেমধ্যে নাটক ও অন্য কিছু করতাম। ব্রিটিশ কাউন্সিলেও নাটক করেছি। তবে লিটল থিয়েটারই এ দেশের প্রথম শিশুদের নাটকের দল। ১৯৭৮-৭৯ সালে মাযহারুল ইসলাম বাবলা ও আমি মিলে দলটি গড়েছিলাম। তিনি আমার সামান্য সিনিয়র। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী নাজমা জেসমিন চৌধুরী সাহায্য করেছেন। উপদেষ্টা ছিলেন সেলিম আল দীন, নাসির উদ্দীন ইউসুফ ও আফজাল হোসেন। রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নাজমা আপা। আমি ও বাবলা ভাই মিলে নির্দেশনা দিয়েছি। তখন মহিলা সমিতিতে শুক্রবার সকাল ১১টায় শিশুদের নাটকের নিয়মিত প্রদর্শনী হতো। সেখানে ৬০-৭০টি প্রদর্শনী করেছি। নাচ-গান মিলিয়ে খুব জমজমাট নাটক ছিল। শিশুরা দলবেঁধে দেখতে আসত। এরপর ‘যেমন খুশি সাজো’ করলাম। তখন আবার নাজমা আপার সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হলো। বাবলা ভাই চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেলেন। ফলে চ্যালেঞ্জটি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ নাট্যরূপ দিলাম, রিহার্সালও শুরু হলো। ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভের কোর্সে আমাদের সঙ্গে চলচ্চিত্র সমালোচক মাহমুদা চৌধুরী পড়তেন। তিনি ভারতে যাওয়ার সময় বললাম, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাকে অনুমতি এনে দিন। আমরা যে নাটকটি করছি, সে কথা তাঁকে জানানোর জন্য বললাম। তিনি তাঁর প্যাডের ওপর সবুজ কালিতে লিখে দিয়েছিলেন—‘ঢাকার লিটল থিয়েটারে এটি মঞ্চস্থ হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। ’ খবরটি ‘কিশোর বাংলায়’ও ছাপা হয়েছিল। তবে লেখাটি হারিয়ে ফেলেছি, সব কিছুই হারিয়ে ফেলি। মূল্যবান চিঠি, প্রথম অ্যাওয়ার্ড কিছুই নেই। ‘আগামী’র জন্য দিল্লিতে খুব সুন্দর ‘সিলভার পিপক’ সম্মাননা পেয়েছিলাম। একটি নাট খুলে গিয়েছিল। বায়তুল মোকাররমের এক দোকানে সারাই করতে দিয়েছিলাম, অনেক দিন পর গিয়ে দেখি, দোকানটি উঠে গেছে।
নাটকটি কেমন চলেছিল?
অনেক দিন চলেছিল, ১ শর বেশি প্রদর্শনী হয়েছে। এরপর ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’, জার্মান কালচারাল সেন্টারের সঙ্গে যৌথভাবে ‘বিজ্ঞ নাথান’সহ কয়েকটি প্রযোজনা করেছি। টানা ২৫ বছর আমি এই সংগঠন পরিচালনা করেছি। ভালোই চলেছে। ১৯৯৩ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলে জাঁকজমকের সঙ্গে ‘রজত জয়ন্তী’ও করেছি। এরপর জাহিদ হাসান শোভন এসে কয়েকটি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছে। শাকিল ফয়জুল্লাহও কয়েকটি নির্দেশনা দিয়েছে। তবে ২০০০ সালের পর থেকে দেখা গেল দলের হাল ধরার মতো কাউকে পাচ্ছি না। আস্তে আস্তে দলটি মরতে শুরু করল। তবে এটিই বাংলাদেশের প্রথম শিশুদের নাটকের দল, যারা মহিলা সমিতিতে বড়দের পাশাপাশি দর্শনীর বিনিময়ে নাটক করেছে।
ছবি দেখা শুরু কিভাবে?
আগে বিচ্ছিন্নভাবে ছবি দেখতাম। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে নিয়মিত সিনেমা দেখা শুরু হলো। তখন আমেরিকান, রাশিয়ান বা ভারতীয় দূতাবাসের কালচারাল সেন্টারে ছবি দেখানো হতো। ফিল্ম ফরম্যাটের ১৬ বা ৩৫ মিলিমিটারের এই ছবি দেখার জন্য কোনো না কোনো ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হতে হতো। ইমেজ ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হয়ে অনেক ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি। তখনই বোধ হলো—সিনেমা সিরিয়াস বিষয়। ছবি দেখার ঘোর থেকেই মনে স্বপ্ন দানা বাঁধল—একদিন ছবি বানাব।
ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন।
এটি ঠিক যে, আমি নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই। সিনেমা বানানোর পাশাপাশি সাংগঠনিক বিষয়গুলোতেও সময় দিই। এ দেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি, দীর্ঘদিন ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। প্রেসিডেন্টও হয়েছি। জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে পাবলিক লাইব্রেরিতে চার্লি চ্যাপলিন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের রেট্রোস্পেকটিভ করেছি, মৃণাল সেনকে এনে তাঁর রেট্রোস্পেকটিভ করেছি। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির এশিয়ার আঞ্চলিক সেক্রেটারিও ছিলাম। তারেক (মাসুদ) আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সে খুব বকাবকি করত, ‘এসব করে তো আপনার ভালোভাবে ছবি বানানো হচ্ছে না, ছবির যত্ন নিচ্ছেন না। সাংগঠনিক কাজগুলো বন্ধ করুন। ’ তবে আমি এগুলোকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। নচেৎ হয়তো আরো বেশি ছবি বানাতে পারতাম, আরো নিখুঁত ছবি হতো, কিছু পয়সা আসত। সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমি কাজগুলো না করলে তো আন্দোলনটি দাঁড়াত না, যে আন্দোলনে আমি বিশ্বাস করি।
কবে শর্টফিল্ম ফোরাম করলেন?
১৯৮৬ সালে, প্রস্তাবটি আমারই ছিল। তারেক ও আমি উদ্যোক্তা, তানভীর (মোকাম্মেল) ভাই তখন দেশের বাইরে। (মানজারে হাসিন) মুরাদ ভাইও বাইরে। তখন তানভীর (মোকাম্মেল) ভাই ‘হুলিয়া’ বানানো শুরু করেছেন। আমার ‘আগামী’ বানানো শেষ। তারেকের এসএম সুলতানের ওপর প্রামাণ্যচিত্রের কাজ চলছে। আমরা উপলব্ধি করেছি, বিচ্ছিন্নভাবে ছবি বানালে হবে না, সবাই মিলে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে না পারলে আমাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না। সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৮৮ সালে ‘আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব’ শুরু করি।
ছবি বানানোর হাতেখড়ি তো ফিল্ম আর্কাইভের কোর্সের মাধ্যমে?
১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স চালু করল। সে কোর্সে পড়তে হলে অন্তত স্নাতক পাস হতে হয়। তবে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে খুব অনুরোধ করে মৌখিক পরীক্ষা দিলাম। কোর্সটিতে ভর্তির জন্য অনেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ৪০ জনকে নিল। আলমগীর কবির, বাদল রহমান, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী মৌখিক পরীক্ষা নিলেন। ১৬ জন পাস করল। কোর্সটি তারেক মাসুদ, আমি, তানভীর মোকাম্মেল, মানজারে হাসিন মুরাদ, শামীমা আখতার, রিনি রেজাও করেছেন। আলমগীর কবির আমাদের সবচেয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। কোর্স শেষ হওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নিলাম—বড় বাজেটের ছবি বানানোর টাকা তো নেই, কম খরচে ১৬ মিলিমিটারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানাব। ফিল্মের দাম, ক্যামেরা ভাড়া, লেমিনেটিং প্রসেসিং চার্জও কম। যেকোনো জায়গায় দেখানোও যাবে।
‘আগামী’র কথা বলছেন?
হ্যাঁ, ১৯৮২ সালের অক্টোবরে শুরু করে ডিসেম্বরে শুটিং শেষ করলাম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখন প্রায় বিলুপ্ত, এরশাদ ক্ষমতায় এসেছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকারের প্রবণতা শুরু হয়েছে। রাজাকারদের পুনরুত্থান ঘটছে, মুক্তিযোদ্ধারা অসহায়। ছবিতে এ পরিস্থিতিই নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। গল্প ও চিত্রনাট্য আমার। ২৫ মিনিটের সিনেমাটি করতে ৭০ হাজার টাকা খরচ হলো। সেই টাকাও আমার ছিল না। লিটল থিয়েটারের এক অভিভাবক নাসিমা ইসলাম ৪০ হাজার টাকা দিলেন। শুটিং করলাম। ধারদেনা করে বাকি টাকা জোগাড় করে ১৯৮৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে অন্য কাজগুলো শেষ করলাম। সেন্সর বোর্ডে জমা দিলাম।
তারা আটকে দিল কেন?
ছবিতে একটি দৃশ্য ছিল—দেশ স্বাধীনের পর গ্রামের কয়েকটি শিশু ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছে, ‘পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী’র বদলে তারা হানাদার বাহিনী দিতে বলল। পাকিস্তানি বললে নাকি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। তবে আমি কিছুই মানলাম না, তখন কেবল তৃতীয় বর্ষে পড়ি। এরশাদের আমল শুরু হয়েছে, সামরিক আইন জারি হয়েছে। সংবাদ সম্মেলন করে বললাম, এই এই কারণে তারা আমার ছবিকে সেন্সর দিচ্ছে না। অনেক সংগঠন ও ৫২ বুদ্ধিজীবী আমার পক্ষে বিবৃতি দিলেন, আনিসুজ্জামানও ছিলেন। তখনকার সবচেয়ে বেশি বিক্রীত পত্রিকা ইত্তেফাকসহ প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পাতায় খবরটি ছাপা হলো। এরপর আপিল বোর্ডে গেলাম। ছাড়পত্র পেয়ে ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ‘আগামী’র ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রথম প্রদর্শনী হলো। মানুষের চাপে পাবলিক লাইব্রেরিতেও শো করলাম। সেখানেও বিশাল লাইন। ১৯৮৫ সালে তানভীর মোকাম্মেলের ‘হুলিয়া’ মুক্তি পেল। এর পর থেকে একসঙ্গে ‘আগামী’ ও ‘হুলিয়া’র শো করতাম। টিকিটের দাম ১০ টাকা। দেশের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে এই দুই ছবির প্রদর্শনী হয়নি, গ্রামেও শো করেছি। টিকিটের বিনিময়ে চাল নিয়েছি। আমার ধারণা, ছবিটির গল্প এত সাধারণ যে সবাই বুঝতে পারত। টেকনিক্যালি দুর্বল হলেও এটি সময়ের চাহিদা, মানুষের চাপা ক্ষোভকে ধরতে পেরেছিল বলে সবাই গ্রহণ করেছে। যে সরকার আটকে দিয়েছিল তারাই ১৯৮৫ সালে দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে ছবিটিকে পাঠাল। উৎসব উপলক্ষে মুম্বাইয়ে সরকারি খরচে সাব-টাইটেল করা হলো। ছবিটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা নির্মাতার ‘সিলভার পিকক’ সম্মাননা পেয়েছে। আমার পক্ষে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।
এরপর তো ‘সূচনা’?
‘সূচনা’ ৬২ মিনিটের ছবি। এ ছবির মাধ্যমেই হুমায়ুন ফরীদি ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সিনেমায় অভিনয়ের শুরু। এটিও মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে, আমারই লেখা। এখনো অনেকে ছবিটির কথা বললেও একটু বেশি বক্তব্যধর্মী বলে আমার পছন্দ হয়নি, সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এরপর করলাম ‘চাকা’।
মূল গল্প তো সেলিম আল দীনের?
লিটল থিয়েটার করতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। নাটকটি ঢাকা থিয়েটার তখন মঞ্চে প্রযোজনা করছিল। আফজাল (হোসেন) ভাই একদিন বললেন, ‘নাটকটি দেখ, ভালো ছবি হতে পারে। ’ এত চরিত্র ছিল যে প্রথমবার দেখে মাথায় ঢুকল না। দ্বিতীয়বার দেখে মনে হলো, মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আমার মতো করে সাজালে এটি ভালো সিনেমা হতে পারে। চিত্রনাট্য লেখা শুরু করলাম। তত দিনে ঢাকা থিয়েটার জেনে গেল, নাটকটি নিয়ে আমি কাজ করছি। একে তারা ভালোভাবে নিল না। ঘোষণা দিয়ে বসল, একে ছবি বানাবে না। ফলে সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মনে আছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাসের ওপর বসে কথা বলেছি। অনুমতি চাওয়ার পর তিনি বললেন, ‘ছবিটি তুই কর অসুবিধা নেই, চিত্রনাট্য আমি লিখব। ’ আমি তো চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছি—এ কথা বলার পর তিনি বললেন, ‘তাহলে সংলাপ লিখে দিই। ’ বললাম, ছবিতে তো সংলাপ নেই বললেই চলে। যা-ও আছে সাধারণ মানের। ’ তখন তিনি রেগে গেলেন, ‘তুই তো আমার কোনো কথাই শুনবি না। যা তোকে অনুমতি দেব না। ’ খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আপনি অনুমতি না দিলেও আমি ছবিটি করব। টাইটেলে সেলিম আল দীনের ‘চাকা’ নাটক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখে দেব। তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। ছবিটিও আপনার নাটক থেকে ভিন্ন হবে। পরদিন ফোন করে তিনি অনুমতি দিলেন।
কিভাবে নির্মাণ করলেন?
পরিচালক হিসেবে পুরো ছবিতে ইচ্ছা করেই দর্শককে বিরক্ত করতে চেয়েছি। একটি লাশ নিয়ে দুই গাড়োয়ান যাত্রা করে। এটি মানবিক গল্প। দীর্ঘ পথের দুই পাশে ফসলের ক্ষেত, অনেক দূরে দূরে গ্রাম—এমন লোকেশন বেছেছি। মাঝখান দিয়ে গরুর গাড়ি চলেছে। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক—এই ছিল বিষয়, সংলাপ খুব কম। এমনভাবে দৃশ্যায়ন করেছি যে দুই গাড়োয়ান লাশ নিয়ে যখন খুব বিরক্ত হবে, তখন দর্শকও বিরক্ত হবে। আবার যখন তারা লাশের সঙ্গে একাত্ম হবে, দর্শকও হবে। গরুর গাড়ির ‘ক্যাচ’, ‘ক্যাচ’ শব্দে দর্শকদের বিরক্ত করেছি। প্রথমদিকে ৩০-৪০ সেকেন্ডের লংশটও নিয়েছি।
রি-অ্যাকশন কেমন ছিল?
৬৫ মিনিটের এই ছবির প্রথম প্রদর্শনী জাদুঘরে হলো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে সেলিম ভাইও এসেছিলেন। তবে বেশির ভাগ বোদ্ধারই মূল্যায়ন খারাপ ছিল—এত স্লো, এ কোনো ছবি হলো? যে দুই-একজন প্রশংসা করলেন, তাঁদের মধ্যে সেলিম ভাইও ছিলেন। তিনি সিনেমা দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, ‘খুব ভালো ছবি বানিয়েছিস। ’ মাহবুব জামিলও প্রশংসা করেছেন। এই ছবির প্রাথমিক দর্শক প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ ছিল, অনেকে খুব সমালোচনাও করেছেন। প্রথমদিকে তো অনেকে বুঝতেই পারেননি। পরে বুঝেছেন কী করতে চেয়েছি। এক শোতে রিকশাওয়ালাকেও দেখেছি টিকিট কেটে ছবি দেখেছেন। বের হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগল? বললেন, ‘মানুষ মরলে যে তার কোনো দাম নেই—বুঝলাম। ’ সাধারণত একই প্রতিযোগিতায় কোনো ছবিকে সেরা ছবি ও সেরা পরিচালকের পুরস্কার দেওয়া হয় না। এ ছবিটি ১৯৯৩ সালে জার্মানির ম্যানহাইম ফিল্ম ফেস্টিভালে ‘ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড’ ও ‘ইন্টার ফিল্ম জুরি অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে। পরের বছর ফ্রান্সের ডান কার্ক ফিল্ম ফেস্টিভালে ‘বেস্ট ফিল্ম’ ও ‘বেস্ট ডিরেকশন’ অ্যাওয়ার্ড, স্টুডেন্ট জুরি অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে। এসব পুরস্কার পাওয়ার পর ছবিটির ব্যাপারে সমালোচকদের ধারণা বদলালো। ১৯৯৩ সালে তৈরি আমার এই ছবিটি খুব বিখ্যাত হয়েছে। আমার সমালোচকদের মতে, এখনো এটি আমার সেরা ছবি।
‘চাকা’র মতো ছবি বানানোর পর কেন শিশুদের ছবি বানাতে গেলেন?
আসলে শিশুদের জন্য ছবি নির্মাণের আগ্রহ আগে থেকেই ছিল। ‘চাকা’ নিয়ে ২০টি চলচ্চিত্র উৎসবে গেছি। সেগুলোতে শিশুতোষ বিভাগে যেসব ছবি আসত, দেখতাম। দেখে মনটাই খারাপ হয়ে যেত, শিশুদের জন্য এত চমৎকার ছবি বানানো হয়, ওরা সেগুলো আনন্দ নিয়ে দেখে। আর আমার ভাষায়, আমার সংস্কৃতির কোনো ছবি তাদের জন্য তৈরি হয় না! এ আক্ষেপ থেকেই ‘দীপু নাম্বার টু’ তৈরিতে হাত দিলাম। তবে গল্পটি ১৯৮৫ সালেই পড়া হয়েছিল, তখনই তৈরির কথা ভেবেছিলাম। তখন মুহম্মদ জাফর ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে থাকতেন। ঠিকানা জোগাড় করে তাঁকে চিঠিও লিখেছিলাম—আপনার ‘দীপু নাম্বার টু’ নিয়ে একটি ছবি বানাতে চাই। চমৎকার ভাষায় তিনি উত্তর দিলেন, ‘অনুমতি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। ’ তবে নানা কারণে কাজে হাত দিতে পারলাম না। ঠিক ১০ বছর পর সরকারি অনুদানে ছবিটি নির্মাণে হাত দিলাম। ‘এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী’র পর এটি অনুদানের দ্বিতীয় শিশুতোষ ছবি। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম। প্রবাসী বাঙালিরা ‘আগামী’ দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। জাফর ভাই ও ইয়াসমিন (হক) ভাবিও দেখলেন। দেখে ভালো লাগায় তাঁরা তাঁদের বাসায় রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ জানালেন। সেদিনই লিখিত অনুমতি নিয়ে নিলাম।
বিখ্যাত উপন্যাসকে ছবিতে রূপ দেওয়া এবং শিশুদের নিয়ে কাজ করা তো খুব চ্যালেঞ্জের…
হ্যাঁ, এ গল্পটি শিশুদের কাছে খুব জনপ্রিয়। তাদের মনে উপন্যাসটির সব চরিত্র ও ঘটনা গেঁথে আছে। ফলে গল্প থেকে খুব বেশি সরে আসার সুযোগ ছিল না। ফলে সাহিত্যের ছোঁয়া যেমন রাখতে হয়েছে, তেমনি আবার আলাদা মাধ্যম বলে সিনেমার দিকটিও দেখতে হয়েছে। চিত্রনাট্য লেখার সময় এই চ্যালেঞ্জগুলো ছিল। কত সহজে গল্পটিকে শিশুদের সামনে ক্যামেরায় তুলে আনা যায় সে চেষ্টাই করেছি। তবে কিছু জায়গায় সিনেমার ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। শিশুদের নিয়ে কাজ করা এক অর্থে সহজ, আবার কঠিনও। অনেকে ভাবেন, শিশুতোষ সিনেমা খুব সহজে বানানো যায়, বাজেটও কম। এটি ভুল ধারণা। বড়দের ফাঁকি দেওয়া যায়, ওদের তো দেওয়া যায় না। ছবি দেখে ভালো লাগেনি—কথাটি তারা মুখের ওপর বলে দেয়। আর ডিটেইল শুটিং করতে গিয়ে খরচও বাড়ে। ছবি বানানোর সময় তারা লোকেশনে যায়, সঙ্গে অভিভাবকও যান। টিম দ্বিগুণ হয়ে যায়।
ওরা তো অভিনয় জানে না। কিভাবে কাজ করান?
শিশুদের ছবিতে যখন কোনো ছেলে-মেয়েকে নিই, সে চরিত্রের জন্য সে উপযোগী কি না সেটি শুধু খেয়াল রাখি। অভিনয় জানে কি না—এ ব্যাপারে একটুও গুরুত্ব দিই না। শুধু তাদের আগ্রহ কতটুকু, ওরা বুদ্ধিমান কি না—তাই খেয়াল রাখি। বুদ্ধিমান হলে তারা আমার কথা সহজেই ধরতে পারে। বুদ্ধিমত্তা থাকলে বিশ্বের যেকোনো নবীন বা প্রবীণের কাছ থেকে অভিনয় বের করে নেব—এই বিশ্বাস আমার আছে। এই ছবির চরিত্রগুলোকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পেয়েছিলাম। শিশুরা তো কাঁচা মাটির মতো, অভিনয়ের কোনো শিক্ষা নেই বলে তারা চরিত্রটি অন্য পাকা অভিনেতার মতো ভেবে বসে না। চরিত্র বুঝিয়ে দিলে সহজে অভিনয় করতে পারে, অনেক ভালো অভিনেতাকেও হার মানিয়ে দেয়। উদাহরণ দিয়ে বলি—আমার কয়েকটি ছবির অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের কিন্তু নিজস্ব স্টাইল দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁকে অভিনয়ের সময় সে স্টাইল থেকে বের করে আনতে হয়। তিনি গুণী অভিনেতা সন্দেহ নেই, তবে বারবার খেয়াল করে দেখেছি—‘আমার বন্ধু রাশেদ’ ছবিতে শেষ দৃশ্যে রাশেদের অভিনয় তাঁর চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। আমি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করেছি। রোকেয়া প্রাচী, সোহানা সাবা আমার তৈরি। সাবার শুরু ‘খেলাঘর’-এ।
‘দীপু নাম্বার টু’র সাড়া কেমন ছিল?
ছবিটি নির্মাণের সময়ই মনে হয়েছিল—এটি খুব ভালো হবে। কারণ যেখানে যা প্রয়োজন, তা-ই করেছি। মিরপুরের আসল পানির ট্যাংকে শুটিং করেছি। এক বিন্দু ছাড় দিইনি। ফলে আয়তন হয়ে গেল দুই ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। বাণিজ্যিক ছবিও এত বড় হয় না। তবে প্রিমিয়ার শোতে দেখলাম, দর্শকরা একে খুব ভালোভাবেই নিলেন। ১৯৯৬ সালে মুৎক্তি পাওয়া ছবিটি ভালোই চলেছে। এখনো কোনো শো বা টিভিতে দেখানো হলে অসংখ্য শিশু আগ্রহ নিয়ে দেখে। আমার আরেকটি হিট ছবি ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ও সরকারি অনুদানে বানানো। এতে আমার নিজের ১৯৭১ সালের জীবনের ছাপ আছে।
তারপর তো ভিন্ন ধরনের ছবি বানালেন ‘দুখাই’।
১৯৮৫ সালে দেশে ঘূর্ণিঝড় হয়। তখন এ খবরটি ছাপা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসে এক লোক তার মা-বাবাকে হারিয়েছে, এবার পরিবার-পরিজনকেও হারিয়েছে। খবরটি পড়ে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, একে নিয়ে বড় আকারে, অনেক বাজেট নিয়ে ছবি করব। প্রথমে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম ফিল্ম ফেস্টিভালের হুবার্ট বালস ফান্ড থেকে ১০ হাজার ডলার পেলাম। সেই টাকায় মহেশখালী, কুয়াকাটার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় গিয়ে মানুষের সংগ্রাম, কষ্টের কাহিনি রেকর্ডারে বন্দি করলাম। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমার ‘চাকা’ জাপানের ফুকুওকা ফিল্ম ফেস্টিভালে গেল। ছবি দেখে উৎসবের পরিচালক ফ্যাক্স করে বললেন, জাপানের ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ল্যাব আপনাকে দিয়ে একটি ছবি তৈরি করতে চায়। ১৯৯৫ সালে আড়াই লাখ ডলার মানে প্রায় এক কোটি টাকার বাজেট দিলাম। তারা রাজি হলো। নেদারল্যান্ডসের সেই প্রতিষ্ঠানও আমাকে কাজ করার অনুমতি দিল। ১৯৯৬ সালের শুরুতে দুখাইয়ের কাজ শুরু করলাম।
কোথায় শুটিং করেছেন?
কুয়াকাটা থেকে ১২ মাইল দূরের চরগঙ্গামতিতে লোকেশন ঠিক করলাম। একেবারে দুর্গম এলাকা, পৌঁছাতে দুই দিন লাগে। শীতকালের শান্ত সমুদ্র ও বর্ষাকালে অশান্ত সমুদ্রের সময়ও শুটিং করেছি। শুটিং করতে গিয়ে ১২০ জনের বিশাল টিম, ক্যামেরা, ক্রেন সব নিয়ে তিন-চার মাইল কাদায় হেঁটেছি, সাইক্লোন শেল্টারে থেকেছি। ঝড়ের পর বৃষ্টিতে ভিজে সত্যিকারের বৃষ্টিকে বন্দি করেছি। ছবিটি ১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছে। সব ছবিতেই পরিশ্রম করতে হয়। ‘দীপু নাম্বার টু’র জন্য পাহাড়, জঙ্গল ঘুরে শুটিং করেছি।
আচ্ছা ‘খেলাঘর’ নিয়ে মাহমুদুল হক কী বলেছিলেন?
তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে ছবিটি দেখার পর খুব যে পছন্দ করেছেন—সেটা মনে হলো না। সরাসরি কিছু বলেনওনি। আসলে লেখককে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন। তবে বিদেশে অনেক বাঙালিই ছবিটি পছন্দ করেছেন। এটি শ্রীলঙ্কার এক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের সম্মাননাও পেয়েছে। কয়েক বছর আগে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক ভারতীয় অধ্যাপক মেইলে বলেছেন, “আমি এখানে দক্ষিণ এশিয়ান সিনেমা পড়াই। আমার কোর্সে অপর্ণা সেনের ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার’, সাবিহা সুমারের ‘খামোশ পানি’ এবং বাংলাদেশ থেকে আপনার ছবিটি পড়াতে চাই। ” উত্তর দিলাম, অবশ্যই। এখনো কেউ জিজ্ঞেস করলে একে আমার অন্যতম প্রিয় ছবি বলি। কারণ যেভাবে বানাতে চেয়েছি, পেরেছি।
হুমায়ূন আহমেদের গল্প নিয়ে তিনটি ছবি করেছেন।
‘দূরত্ব’ ছোটদের হলেও বড়দের জন্যও অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। ‘প্রিয়তমেষু’ একটু ভিন্ন ধরনের গল্প। মেয়েদের নির্যাতন ও রুখে দাঁড়ানোর গল্প। তবে ছবিটির শুরুতে খুব ঝামেলা হয়েছিল। কারা যেন রটিয়েছিল, হুমায়ূনের অনুমতি ছাড়াই আমি কাজ শুরু করছি। এক দিন সরাসরি তাঁর বাসায় চলে গেলাম। চেকে টাকার অঙ্কের দিকে না তাকিয়ে বললেন, ‘কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে বলুন। ’ অনুমতি পেয়ে গেলাম। তবে ‘অনিল বাগচীর একদিন’-এর অনুমতি তিনি দিয়ে যেতে পারেননি, পরিবার থেকে নিয়েছি। দর্শকরা পছন্দ করলেও ছবিটি ভালো চলেনি। কারণ প্রযোজক বেঙ্গল গ্রুপ ছবির পেছনে খরচ করলেও তেমন প্রচারণা চালায়নি। জোর করে আমিই যা করিয়েছি।
সাহিত্যিকদের গল্প কেন নেন?
নিজের চিত্রনাট্যে যেমন ‘আগামী’, ‘সূচনা’, ‘দুখাই’ করেছি, তেমনি অন্যদের গল্প নিয়েও কাজ করি। আসলে আমি আইডিয়া খুঁজি। গল্পটি পড়ার পর সেটি যখন নাড়া দেয়, তাড়িয়ে বেড়ায়, সেই গল্প নিয়ে ছবি বানানোর তাগিদ বোধ করি, ছবি বানাই। একদিক থেকে এটি কঠিন কাজ, অন্যদিক থেকে বললে ভালো গল্প পেলে আমার কাজটি সহজ হয়ে যায়। তবে এ-ও ঠিক, সবাইকে সন্তুষ্ট করে ছবি বানানো যায় না। সত্যজিৎ রায়ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তুষ্ট করতে পারেননি।
‘আঁখি ও তার বন্ধুরা’র কতটুকু কাজ বাকি?
এ-ও জাফর ইকবালের গল্প, এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেয়ের গল্প। আমার ধারণা, এটি মজার ছবি হবে। সব ঠিক থাকলে কোরবানি ঈদে ছবিটি মুক্তি দেব।
শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের ভাবনাটি কেন এলো?
ভারতের দিল্লিতে গিয়ে এই ভাবনার শুরু হয়েছিল। সেখানে দেখেছিলাম—শিশুদের বেশ বড় কয়েকটি চলচ্চিত্র সংসদ আছে। স্ত্রী (মুনিরা মোরশেদ) ও আমি মিলে ২০০৪ সালে উদ্যোগ নিলাম। মুহম্মদ জাফর ইকবাল সভাপতি ও মুস্তাফা মনোয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হলেন। ২০০৬ সালে গড়ে উঠল এই সংসদ। ২০০৮ সাল থেকে আমরা নিয়মিতভাবে ‘আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব’ করছি। সেখানে বিভিন্ন দেশের শিশু চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয়। নানা বয়সের শিশুদের বানানো ছবির প্রতিযোগিতাও হয়। এ উৎসবে আমরা সারা দেশ থেকে শখানেকের ওপর চাইল্ড ডেলিডেগস নিয়ে আসি। তারা কর্মশালা ও উৎসবে অংশ নেয়। বিভিন্ন দেশ থেকেও শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতারা আসে। এবার দশম উৎসব হলো। পঞ্চম উৎসবে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন—প্রতিবছর একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হবে। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন।
সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাতার জীবন কতটা সংগ্রামের?
অনেকটাই, এখনো ফান্ড জোগাড় করতে কষ্ট হয়। সরকারি অনুদানের সঙ্গে আরো টাকা জোগাড় করে ছবি বানাতে হয়। সে জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়। নিয়মিত ফান্ড পেলে প্রতিবছর একটি করে ছবি তৈরি করতে পারতাম। এখন দুই-চার বছর পর পর বানাতে হয়। ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ ২০১১ সালে মুক্তি পেয়েছে, পরের ছবি ‘অনিল বাগচীর একদিন’ ২০১৫ সালে। সংগ্রাম করতে হবে জেনেই তো এ পথে এসেছি। ১৯৮৬ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ থেকে পাস করেছিলাম, তখন আমাদের বিভাগের সামনে পোস্টার লাগানো থাকত—‘জয়েন ফার্মাসি টু গো আমেরিকা। ’ যুক্তরাষ্ট্রও প্রচুর ফার্মাসিস্টের ভিসা দিচ্ছিল। আমার বেশির ভাগ বন্ধুই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রবাসী। তত দিনে আমি দুটি ছবি বানিয়ে ফেলেছি। এ অবস্থায় মনে হলো, এখন কী করব? পেশাগত জীবনে যোগ দিতে না পারলে তো অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ব। অনেক ভেবে বড় এক ফার্মাসিউটিক্যাল কম্পানিতে যোগ দিলাম। আমাদের শেরাটনে প্রশিক্ষণ শুরু হলো। টাই, স্যুট পরে সারা দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হলো না। মনে হলো, আমার জীবন তো শেষ। পরদিন পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে চলে এলাম। তখন কিন্তু বিয়ে করেছি। জেনেশুনেই তো আমি এই পথ বেছে নিয়েছি।
শ্রুতলিখন : সাইদ হাসান রাজ
(১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
সময় টেলিভিশন, কারওয়ানবাজার, ঢাকা)