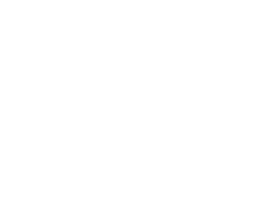যেখানে সবাই পণ্ডিত সেখানে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে লাভ নেই
বন্য প্রাণীর পেছনে সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাদের খোঁজে চষে বেড়িয়েছেন সারা দেশ। তাদের নিয়ে বই লিখেছেন। কাজ করেছেন দুবাই চিড়িয়াখানায়। এখন দুবাই সাফারিতে আছেন। ড. রেজা খান বাংলাদেশের বন্য প্রাণী নিয়ে খোলামেলা বলেছেন। তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন ওমর শাহেদ। ছবি তুলেছেন কাকলী প্রধান

আপনি তো সালিম আলীর ছাত্র?
১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করি। আর ১৯৭৩ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই। আমার শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেনের সুপারিশে ভারতের পাখিবিশারদ ড. সালিম আলীর সঙ্গে ‘বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে (বিএনএইচএস) সালিম আলী-লোক ওয়ান থো অরনিথোলজিক্যাল রিসার্চ ফান্ড’-এ পাখির ওপর মাঠ গবেষণা করে পিএইচডি করেছি। উপমহাদেশের ‘পাখিতত্ত্বের জনক’ ড. সালিম আলীর আগ্রহে ‘ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ ফ্লাইক্যাচার’ নিয়ে কাজ করেছি। এটি এমন এক প্রজাতি, যার সম্পর্কে খুব কমই বাস্তব তথ্য ছিল। একে বিরল প্রজাতির পাখি বলা হতো। কীটভুক হলেও বাসা বানানোর স্বভাব আমাদের দেশের ছোট সাঁতারে পাখির মতো। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে দাক্ষিণাত্য পর্বতমালার পাঁচ হাজার ৭০০ ফুট উঁচু পাহাড়ি কুনুর শহরে আস্তানা গাড়লাম। ১৫ দিন মাঠে কাটানোর পর বুঝলাম, পাখিটি মোটেও বিরল নয়। তবে দাক্ষিণাত্যের ‘সোলা’ বা চিরসবুজ বনে মাটির কাছে অন্ধকার ঝোপে বাস করে এবং ক্বচিৎ খোলা জায়গায় এসে পোকা ধরে বলে সচরাচর চোখে পড়ে না। এ তথ্যে সালিম স্যার খুব অনুপ্রাণিত হয়ে আড়াই বছর মাঠের কাজের সময় তিনবার আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এরা গান গায়, যে তিন ধরনের শব্দ করে, সেগুলো দিয়ে পাখিটিকে চেনা যায়, সেগুলো রেকর্ড করলাম। পাখিটি শুধু দাক্ষিণাত্য পর্বতমালার মহিশূর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এলাকার তিন হাজার থেকে আট হাজার ৩০০ ফুট পাহাড়ি বনে পাওয়া যায়। এটি আমাদের চটক, লেজ নাড়ানো, পাখা ঘোরানি, সিপাহি দলের পাখি।
ঢাকায় ফিরলেন কবে?
১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে ফেরার দেড় মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার থেকে সহকারী অধ্যাপক করা হলো। এর পর থেকে হাতি, বাঘ, ভল্লুকসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী নিয়ে প্রচুর গবেষণা শুরু করলাম। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিটিভিতে সপ্তাহে একবার ২৫ মিনিটের ‘এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে’ অনুষ্ঠানটি করেছি। বাচ্চাদের অনুষ্ঠান হলেও সবাই দেখত। সবাই চিনত। ফলে মফস্বলে কোনো দিন সরকারি রেস্টহাউসে থাকার জন্য পারমিশন নিতে হয়নি। সহকারী অধ্যাপকের সর্বোচ্চ ১৬ ঘণ্টা লেকচারের নিয়ম থাকলেও রুটিন কমিটিতে ছিলাম বলে পাঁচ দিনই থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিতাম। যাতে কেউ বলতে না পারে তিনি রুটিন কমিটিতে আছেন বলে ক্লাস কম নিয়েছেন। দুপুরের মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল শেষ করে দুই দিন মাঠে যাওয়া শুরু করলাম। তখন এটি কেউ পছন্দ করতেন না। ফলে খুবই সমস্যা হয়ে গেল। মানে তাঁদের রাজনৈতিক কাজে আমাকে খুঁজে পান না। কোথাও দল ভারি করে যাবেন, আমি নেই। হ্যাঁ, কোনো শিক্ষক অসুস্থ হলে দেখতে যেতাম, সামাজিক কাজে অংশ নিতাম। এরশাদের আমলে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা শেখার জন্য উর্দুর প্রচলন করা হচ্ছিল, যে কয়জন অধ্যাপক এর বিপক্ষে স্বাক্ষর দিয়েছেন, তার মধ্যে আমিও একজন। এ ধরনের সমস্যায় উপস্থিত থাকতাম। এর বাইরে কোনো দিন কোথাও যাইনি। শুধু থিসিস নয়, ননথিসিসের এমনকি চাইলে যেকোনো বিভাগের ছাত্রদেরও মাঠে নিয়ে ফিল্ড ওয়ার্ক করাতাম। প্রজেক্ট ছিল, প্রজেক্ট বাসে ঘুরেছি। কখনো প্লেনে যাইনি, ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে যাইনি। ট্রেনে থার্ড ক্লাসে গিয়েছি, যাতে সে টাকায় তিন গুণ কাজ করা যায়, আরো ট্রিপ করতে পারি। তখন প্রকৃতিতে যেসব ভাসমান উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তাদের চেনানোর লোক খুব কম ছিল। ওয়াইল্ড লাইফের ওপর ‘এনিমেল হ্যাবিটেট’ নামে একটি কোর্সও রেখেছিলাম। কিন্তু পড়াতাম ‘ফরেস্ট্রি অব বাংলাদেশ’। তবে আমি চলে যাওয়ার পর কোর্সটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বিভাগের জাদুঘরের জন্য প্রচুর কাজ করেছি। যেমন কালো শালিক ও বড় সি গাল বা জল কবুতরের নমুনা সেন্ট মার্টিনস থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছি। সেন্ট মার্টিনসসহ অনেক জায়গা থেকে অনেক পাখি এনে দিয়েছি। তখন বিচিত্রায় ‘প্রতিবেশ-পরিবেশ’ নামে কলাম লিখতাম। অনেক কাভার স্টোরিও করেছি। দৈনিক বাংলা, অবজারভারে লিখেছি। বাংলাদেশ টাইমসেও মাঝেমধ্যে লিখেছি। সহকারী অধ্যাপকের বেতন ১৮০০, বিটিভিতে প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য ৫০০, পত্রপত্রিকায় লিখে ২০ টাকা, বিচিত্রা কাভার স্টোরির জন্য ১০০ থেকে ২০০ টাকা দিত। দুটি বাচ্চা আছে, যেহেতু দৌড়ঝাঁপ করি, সব মিলিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্টের ছিল। ঘুমানোর ছয় ঘণ্টা বাদে পরিবারের কারো সঙ্গে দেখা হতো না। এত কষ্ট করার একটিই কারণ ছিল—যদি সহযোগী অধ্যাপক হই, তাহলে বেতন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা বাড়বে। তখন টাকার ঘাটতি আর থাকবে না। টিভিতে প্রোগ্রাম রাখলেই চলবে, লেখার দিকে মনোযোগ দিতে পারব। বন্য প্রাণী বিষয়ে তখন আমি দেশে এক নম্বর। কারো কাছে এক বা দুজন থিসিসের ছাত্র, আমার তখন চারজন, এমফিলের জন্য দুজন। আমি কিন্তু সহকারী অধ্যাপক। ছাত্ররা পছন্দ করত। কারণ তাদের সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্ক করতাম, যেটা অন্য কেউ করতেন না। সবাই ঘরে বসে থাকতেন। ছাত্রদের লেখার ইংরেজি কারেকশন করে দিতেন। তারা ফার্স্ট হতো, শিক্ষকের নামও ছাপা হতো। কিন্তু আমি বললাম, নো, আই উইল নট ডু ইট। যদি তোমাদের সঙ্গে মাঠের কাজে অংশ না নিই, তাহলে লেখক হিসেবে নাম দিতে পারবে না। ১৯৮২ সালে সহযোগী অধ্যাপকের কয়েকটি পদ ঘোষণা করা হলো। ১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হলো। প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে আরো কয়েকজন আবেদন করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আমার বই ‘ওয়াইল্ডলাইফ অব বাংলাদেশ—অ্যা চেকলিস্ট’ প্রকাশ করেছে, ইন্ডিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখা বেরিয়েছে, আন্তর্জাতিক জার্নালেও লেখা আছে। তখন নিয়ম ছিল, সহকারী থেকে সহযোগী অধ্যাপক হতে হলে চারটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে—দেশে ছয়টি থাকতে হবে, সেখানে আমার ১৫ থেকে ২০টি ছিল। শামসুল হক সাহেব ভিসি হওয়ার মাত্র সাত দিনের মাথায় ইন্টারভিউয়ের তারিখ ফেলা হলো, যাতে নতুন ভিসি প্রার্থীদের সম্পর্কে কিছু বুঝতে না পারেন। কোনো চক্রান্ত নিশ্চয়ই কাজ করেছে। ১৯৭৩ সালের ২৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার ঠিক ১০ বছর পরে ২৬ নভেম্বর ১৯৮৩ ইন্টারভিউ হলো। ইন্টারভিউ শেষে ভিসি অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। বোর্ড থেকে যিনি প্রথম বের হবেন তাঁকে জিজ্ঞেস করব, কার চাকরি বা প্রমোশন হয়েছে? আজও কারো পক্ষে এ কথা ইন্টারভিউ বোর্ড মেম্বারকে জিজ্ঞাসার সাহস হবে না। প্রথমে বেরিয়েছিলেন সম্ভবত বায়োলজির ডিন, তিনি সয়েল সায়েন্সের শিক্ষক ছিলেন, নামটি মনে নেই। স্যার বেরিয়েই বললেন, ‘রেজা, স্যরি তোমাকে করতে পারিনি।’ বললাম, কাকে করেছেন? তিনজনের নাম বললেন। তখন বললাম হ্যাঁ, এটাই হওয়ার কথা। বিভাগের সিদ্ধান্ত জানতাম—তাঁরা এই তিনজনের নাম প্রস্তাব করেছেন। তিনজনের একজন যে ল্যাবরেটরিতে ডক্টরেট করেছেন, সেই ল্যাবরেটরির নিজস্ব ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। সেই একটি লেখার ভিত্তিতে তাঁকে সহযোগী অধ্যাপক করা হয়েছে! তাঁদের কারো নাম বলতে চাই না। কারো যাচাইয়ের ইচ্ছা হলে যাচাই করতে পারেন। পরদিনই দরখাস্ত করলাম, দুই বছরের ছুটি দেওয়া হোক। জুলাই থেকেই তো আরব আমিরাতের আল আইন চিড়িয়াখানায় কিউরেটরের চাকরি হয়েছে। ভিসাও হয়েছে। সেখানে আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন সালিম আলী। ১৯৮৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর সকালে জয়েন করলাম। দ্যাট ওয়াজ মাই লাস্ট জয়েনিং ডেট।
চিড়িয়াখানাবিরোধী হয়েও আল আইন ও দুবাই চিড়িয়াখানায় ৩৩ বছর কাজ করেছেন?
প্রথমে অশান্তিতে ছিলাম। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, শিক্ষকতায় ফিরব না। স্ত্রীর পরামর্শে ঠিক করলাম, চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা শিখব। আল আইনে প্রথমে পাখি, পরে বানর-হনুমানের ওপর কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা কিউরেটর ফর বার্ডস অ্যান্ড প্রাইমেটসের দায়িত্ব দিল। চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা শিখলাম। জেনেছি, বন্য প্রাণী মানেই লোহার খাঁচার মধ্যে আটকে রাখতে হবে তা নয়, বরং তাদের ছোট্ট শিশুর মতোই যত্ন নিতে হবে। ১৯৮৯ সালে দুবাই চিড়িয়াখানার প্রধান হিসেবে চলে এলাম। এই চিড়িয়াখানার কোথায় কোন গাছ লাগানো হবে সে পরিকল্পনা আমার। দুবাই চিড়িয়াখানায় ২৭ বছর কাজের মেয়াদ এ বছর শেষ হবে। এই চিড়িয়াখানার পরিধি বাড়াতে চার বর্গকিলোমিটারজুড়ে ‘দুবাই সাফারি’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমার দায়িত্ব হবে, পার্কের বন্য প্রাণীর ব্যবস্থাপনা এবং দুবাই ও আমিরাতের বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রতি বুধবার সাফারিতে গিয়ে বন্য প্রাণী নিয়ে গবেষণা করি। শুধু দুবাই নয়, আরব আমিরাতের বিভিন্ন অঞ্চলেও যাই।
আমাদের চিড়িয়াখানার কিভাবে উন্নয়ন সম্ভব?
কথায় আছে, ‘গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না’, আমার অবস্থা অনেকটা সে রকম। শীতে টিকিট কেটে চিড়িয়াখানায় পাখি দেখতে যাই। চিড়িয়াখানার অনেকেই খবর পেয়ে দেখা করতে আসেন; কিন্তু কোনো দিন কোনো ব্যাপারে ধারণা নিতে চান না। কারণ আমরা সবাই পণ্ডিত। যেখানে সবাই পণ্ডিত সেখানে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে লাভ নেই। তাই আমিই শেখার চেষ্টা করি। শুধু বলব, যদি বলা হয় এক নম্বর হলো সবচেয়ে ভালো আর ১০ নম্বর হলো সবচেয়ে খারাপ, তাহলে বাংলাদেশের চিড়িয়াখানাগুলো ১০ নম্বরে পড়বে। কিছু ভবন বানানো ছাড়া এখানে প্রাণীর জন্য কিছু করা হয়নি। বনের প্রাণীরা তো দালানে থাকে না। দালান বানালে সেটি এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে দেখে মনে হয় এটি বনেরই অংশ।
দুবাইতে বই লিখেছেন শুনেছি।
১৯৮৯ সালে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পর থেকে প্রতি বুধবার ও সপ্তাহান্তে ফিল্ড ওয়ার্ক করে পাখি দেখি, সাপ, টিকটিকি, পোকামাকড় খুঁজি, প্রজাপতির ছবি তুলি। এই করে ‘ইন্ডিজিনাস ট্রিজ অব দ্য ইইউ’ নামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদি গাছের ওপর একটি বই লিখেছি। সেটি দুবাই সরকার প্রকাশ করেছে। ইংরেজি সংস্করণ আমার লেখা, আরবি তাদের। পরের বছর ‘ওয়াইল্ড ক্যাটস অব দ্য ইইউ’। ২০০৮ সর্বশেষ সালে বেরিয়েছে ‘বার্ডস অব দুবাই : অ্যা পিকটোরিয়াল গাইড’। ‘ইন্ডিজিনাস ট্রিজ অব দ্য ইইউ’-এর জন্য ২০০১ সালে ‘নাহিয়ান বিন অ্যাওয়ার্ড ফর ন্যাচারাল হিস্ট্রি’ পেয়েছি।
বাংলাদেশের বন্য প্রাণীর গাইডটি কিভাবে লেখা?
দেশ থেকে যাওয়ার আগে লেখা ‘ওয়াইল্ডলাইফ অব বাংলাদেশ অ্যা চেকলিস্ট’ নামে ১৭৪ পৃষ্ঠার বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২ সালে প্রকাশ করেছে। তাতে সাদাকালো ও কয়েকটি রঙিন ছবি ছিল। এখানে এ ধরনের কোনো বই ছিল না। প্রথমে ৮০০ বা ৮৮৬ প্রজাতির প্রাণী ছিল। ২০১০ সালে ১০৫০টি প্রজাতি নিয়ে এটি রিপ্রিন্ট করেছি। সাহিত্য প্রকাশ বের করেছে। যত প্রাণী বাংলাদেশে দেখেছি, নতুন রেকর্ড করেছি, সব ওই বইয়ে আছে। ২০১৫ সালে এটি বের হয়েছে ‘ওয়াইল্ডলাইফ অব বাংলাদেশ—চেকলিস্ট অ্যান্ড গাইড’ নামে। ছায়াবীথি প্রকাশ করেছে। এটি বাংলাদেশের বন্য প্রাণীর চেকলিস্ট-কাম-গাইড বই। ৫৬৮ পাতার বই। আমাদের বন্য প্রাণীর ওপর এত বড় বই এখনো বের হয়নি। এর মধ্যে প্রাণীগুলোর বাংলা নাম দেওয়া আছে। প্রথম ২০ পৃষ্ঠা বনাঞ্চল ও বাংলাদেশের বন্য প্রাণীরা কোথায় বাস করে, সেন্ট মার্টিনসের ওপর ছোট্ট নোট আছে। হাওরাঞ্চলের ওপর ছোট্ট নোট আছে। এ ধরনের কাজের তো কেউ কখনো চিন্তা করেনি। বন্য প্রাণী বলতে বনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দুটি মিলিয়েই লেখার চেষ্টা করেছি। প্রাণীর বাংলা-ইংরেজি নাম, জিওলজিক্যাল নাম ও তার সম্পর্কে গাইডে একটু বর্ণনাও দেওয়া আছে।
বাংলাদেশের বন্য প্রাণী কিভাবে লেখা?
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই নিজস্ব বন্য প্রাণীর ওপর বই আছে। ১৯৭৭ সালে দেশে ফিরে দেখলাম, ছাত্র বা ভবিষ্যতে যারা শিক্ষক হবে তাদের জন্য তেমন কোনো বই আমাদের নেই। বিদেশি বই, এখানে যা আছে, সেগুলো ঘেঁটে, ইংরেজ আমল থেকে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, ব্যক্তিগতভাবে যেটুকু ঘুরে দেখেছি, সেসব মিলিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে লিখতে শুরু করি। ১৯৮৩ সালে লেখা প্রায় শেষের দিকে ছিল; কিন্তু তখন বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হই। ফলে এক-দেড় বছর নষ্ট হলো। ওখানকার চাকরি ঠেকিয়ে কাজ করতে হলো। ১৯৮৫ সালে এটি বাংলা একাডেমিতে জমা দিলাম। তারা ১৯৮৭ সালে তিন খণ্ডে বইটি বের করে। বাংলাদেশের বনাঞ্চল বা বন্য প্রাণীর পরিবেশ, উভচর ও সরীসৃপ—এই তিন অংশ নিয়ে লেখা এই বইয়ের প্রথম খণ্ড ‘বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর পরিবেশ’। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু পাখি। যেহেতু এখানে পাখির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়, ৫৫৬ কি ৫৫০টি প্রজাতির পাখির কথা দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছি। আর ২৫০-৩০০টি প্রজাতি সম্পর্কে বিশদভাবে বলা আছে। বাকিগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, এসব পাখি আমাদের দেশে আছে। তৃতীয় খণ্ডে আছে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট। বইটি সবাই পড়ছে। কারণ বাংলাদেশের বন্য প্রাণী বা বন ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার এ বই ছাড়া বাংলায় আর কোনো বই নেই। এ বই কেন সাদামাটা ভাষায় লিখেছি সে জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হয়েছে। বলেছি, পাঠ্য বই লেখিনি, যেভাবে কথা বলি সেভাবে লিখেছি, যেন ছাত্ররা সহজে তথ্যগুলো হজম করতে পারে। বইটি পড়ে কী বলতে চেয়েছি, সেটি যেন যে কেউ বুঝতে পারে। এ ছাড়া ‘বাংলাদেশের সাপ’, ‘বাংলাদেশের চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা’ আছে। সুন্দরবনের ওপর ‘সুন্দরবনস’ নামে বড় একটি বই এডিট করেছি, তাতে আমার কয়েকটি লেখাও আছে। আর আইইউসিএনের লাল তালিকার আট ভলিউমের বইয়ের আমি চিফ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ছিলাম।
আমরা বন্য প্রাণীর দিক থেকে কতটা সমৃদ্ধ?
অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অনেক প্রাণী হারিয়েছে, অনেকগুলো সংকটপূর্ণ বা মহাসংকটপূর্ণ হলেও এখনো এখানে যে পরিমাণ বন্য প্রাণী আছে, ইউরোপের অনেক দেশে তার অর্ধেক প্রজাতিও নেই। সে অর্থে এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধনী। এখনো হাঁটলে ঢাকার মতো শহরেও অসংখ্য পাখপাখালি দেখা যায়। পোকামাকড় থেকে কীটপতঙ্গ সবই তো বন্য প্রাণী। বিদেশে এমন অনেক শহর আছে—সারা দিন হাঁটলেও পোকা, প্রজাপতি দেখা যাবে কি না সন্দেহ। তবে আমাদের ব্যবস্থাপনায় দারুণ ত্রুটি রয়ে গেছে। বন বিভাগ মনে করে, বন্য প্রাণী তাদের সম্পদ। তাই একে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ছাড়লেই তাদের কাছ থেকে সম্পদ হারিয়ে যাবে। এ মনোভাব ধরে রাখায় আমাদের চেয়ে ছোট দেশ শ্রীলঙ্কা, নেপালেও বন্য প্রাণীর যে উন্নতি হয়েছে, আমাদের তা হয়নি। নেপালে এ খাতে পর্যটনের মাধ্যমে যত টাকা আয় হয়, তার এক ছটাকও আমাদের হয় না। দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। নিয়মনীতি কাগজে লেখা আছে, বাস্তবে প্রয়োগ নেই। ফলে মানুূষ জানে না যে এই পাখি সে ধরতে পারবে কি না। সরকারি অফিসারের দায়িত্ব, কর্তব্য, তিনি কী করতে পারবেন আইনে বলা আছে। কিন্তু তিনি যদি বাঘ মারেন, তাহলে তাঁর শাস্তি কী হবে তা কিন্তু আইনে বলা নেই। তাঁরা যদি কাঠ চুরি করেন, প্রাণী চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে কী করতে হবে আইনে নেই। এমন আইন বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রক্ষার জন্যই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি বন বিভাগকে মহাসংকটাপন্ন প্রাণীর তালিকা ‘রেড লিস্ট’ করতে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, বন্য প্রাণীর জন্যও বহু টাকা দিয়েছে; কিন্তু বনের জন্য কোনো দিন টাকা আসবে না। এই স্বর্ণের খনি তারা হারাতে চায় না। তাদের কেউই বন্য প্রাণী বিষয়ে পারদর্শী না হলেও জায়গাটি দখল করে রেখেছে। সে জন্য বলেছি, বন্য প্রাণী রক্ষা ও গবেষণার জন্য বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তরের সমমানের আলাদা ক্যাডার সার্ভিস তৈরি করতে হবে। বন্য প্রাণী বিভাগ তৈরি করতে হবে। সেই বিভাগের অধীনে বন বিভাগকে ভেঙে বাণিজ্যিক বা সামাজিক বনায়ন, বনের গাছপালা রক্ষা ও যেসব বন ধ্বংস করা হয়েছে, সেগুলো নতুনভাবে তৈরির জন্য বন সংরক্ষণ ও বন্য প্রাণী বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিভাগ করতে হবে। যদি আলাদা বিভাগ করা হয়, তাহলে শ্রীলঙ্কা, নেপালের বন্য প্রাণী বিভাগের মতো এটিও আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, সেন্ট মার্টিনস, পাহাড়ি এলাকা, জলপ্রপাত, অসংখ্য প্রজাতির প্রজাপতি, পাখি, মাছ, প্রাণী থাকার পরও অব্যবস্থাপনায় আমাদের সব হারিয়ে যাচ্ছে। বন বিভাগের কেউ বিদেশে ট্রেনিংয়ে গিয়ে একাশিয়া, ইউক্যালিপটাসগাছ সেখানে ভালো হয় দেখে এখানে নিয়ে এসেছে। দেখেছে তেলাপিয়ার চাষ হয়, নিয়ে এসেছে। অথচ তেলাপিয়া আফ্রিকান মাছ। থাইল্যান্ডে গিয়ে মাগুরের চাষ দেখে মাগুর নিয়ে এসেছে। এদের কারণেই বাংলাদেশের বন্য প্রাণী এখন বিপন্ন। তারা জানেই না, একাশিয়া ফুলের পরাগায়ণের জন্য এ দেশে কোনো প্রজাপতি নেই, এর আশপাশে গাছ বা ঝোপ হয় না। ফলে সেখানে প্রাণীরা থাকতে পারে না।
সাধারণ মানুষকে কিভাবে সচেতন করা যাবে?
রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে পাঠ্য বইতে লিখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ মাদ্রাসায় পড়ে। অথচ তারা প্রকৃতি, পরিবেশ, বন্য প্রাণী সম্পর্কে সচেতন নয়; কিন্তু বড় বড় দেশে এ সম্পর্কে গির্জায় মিটিং করা হয়। ছেলেমেয়েদের পরিবেশবিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য বনজঙ্গলে পাঠানো হয়। আমাদের দেশে এটি এখনো শুরুই হয়নি। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডায় ধর্মগ্রন্থে বন্য প্রাণী সম্পর্কে যেসব বাণী আছে, সেগুলো অবশ্যই তুলে ধরা দরকার। ছোট্ট উদাহরণ দিই—হাতির ওপর আমার একটি বই ‘বাংলাদেশের হাতি’—এ প্রতিটি ধর্মে হাতি সম্পর্কে কী বলা আছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বন্য প্রাণী গবেষকরা ধর্মের বাণীগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরলেই আসলে বন্য প্রাণীর প্রতি মানুষের মমত্ব বাড়বে।
রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের জন্য কতটা ক্ষতিকর?
ধরে নিচ্ছি এতে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে শূন্য; কিন্তু যদি পর্যটনের জন্য এর ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয় বা এক থেকে পাঁচ হাজার নৌকা চলে অথবা জাহাজ চলাচলের ফলে কয়লা বা তেলের বর্জ্য পড়ে বা জাহাজডুবি হয়, তার সবই সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকর হবে। সুন্দরবন কিন্তু একটি পরিপূর্ণ বন নয়। শালবন ও মিশ্র চিরসবুজ বনের চেয়ে এখানে মোবাইল ফরেস্টই বেশি। সাগরের দিকে যত জমি উঠবে বন সেদিকে যাবে। পেছনের মানে উত্তর অংশ ক্রমাগত উঁচু হয়ে বাদাবনের চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। হাজার বছর পরে এ বনের চেহারা একবারেই বদলে যেতে পারে। এ ছাড়া চরাঞ্চল বৃদ্ধির ফলে এ বন সাগরের দিকে ধাবিত হবে। সুন্দরবনের ভূমি গঠন শক্ত নয়। দক্ষিণের সব এলাকা প্রায় একই রকম। দক্ষিণাংশে যত চর পড়বে, উত্তরাংশ তত শক্ত হবে। ফলে উত্তরাঞ্চল উঁচু হবে। তখন এ বন আর থাকবে না। কারণ জোয়ারের পানি উঁচু জায়গায় পৌঁছবে না। সুন্দরবন ট্রানজিশনাল স্টেজে আছে। একে কখনো পরিপক্ব বা স্থায়ী হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না। কাজেই হাজার চেষ্টা করেও আরেকটি সুন্দরবন তৈরি করা সম্ভব নয়, পৃথিবীতে কেউ পারেনি। অন্যান্য দেশের ম্যানগ্রোভ বনগুলো এক বা দুই প্রজাতির গাছ নিয়ে, আর বাংলাদেশের সুন্দরবন তিন শরও বেশি প্রজাতির গাছ নিয়ে তৈরি। এর একটি প্রজাতিরও যদি ক্ষতি হয়, এখানে ‘সুন্দরবন ক্রো’ নামে একটি প্রজাপতির সাবস্পেসিস আছে, তার যদি কোনো ক্ষতি হয়, আর পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যে কম্পানিগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্র করার জন্য ইআইএ [এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট] করেছে, সেটি এখানকার বা তাদের কোনো প্রতিষ্ঠান বা তাদের সমর্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান করেছে। নিশ্চয়ই এটি কোনো না কোনো দোষে দুষ্ট। বাংলাদেশ বা ভারতীয় কম্পানির বাইরে কোটি টাকা খরচ করে হলেও নিরপেক্ষ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইআইএ করতে দেওয়া হোক যে সুন্দরবনে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে বনের ক্ষতি হবে কি হবে না। যত দিন এমন কোনো রিপোর্ট না আসে তত দিন রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হওয়া উচিত নয়। এক রাম্পালের মতো ১০টি রামপাল করার মতো বহু জায়গা আছে। সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র করা যায়। এটি সরকারের ইচ্ছার ব্যাপার। একে সরিয়ে নিলেই ভালো হবে বলে মনে করি। কারণ এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কেউই জানে না। এখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র করলে যদি ভালোই হবে, তাহলে ভারতের সুন্দরবনের অংশে না করে বাংলাদেশে কেন করছে? এটি আমজনতার প্রশ্ন। ভারত সরকারের কয়লা দিয়ে যদি ভালো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে করছে না কেন? সেখানে তো এখনো লোডশেডিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে মানুষের বসতি আছে, আমাদের সুন্দরবনের ১ শতাংশেও বসতি নেই। আমাদের ৯৯.৯ শতাংশ সত্যিকারের বন; কিন্তু ওদের বন মাত্র ৫০ শতাংশ। তা ছাড়া তাদের মিঠা পানির স্রোত কম বলে গাছের মানও উন্নত নয়। সুন্দরবনের ১০ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে আমাদের ছয় হাজার, তাদের চার হাজার। তাদের চেয়ে আমাদের প্রাণীও বেশি। রামপাল সব দিক থেকে সুন্দরবনের ক্ষতি করবে এতে কোনো দ্বিধা নেই। কারণ ১০ হাজার বছর আগে মহাহিমবাহ বা গ্ল্যাসিয়েশন হয়েছিল। তখন সাগরের পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং বিশ্বে বরফের পরিমাণ বাড়ে, যা প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এখন আমরা আন্তমহাহিমবাহের পর্যায়ে আছি। আরেকটি হিমবাহ কখন হবে কেউ বলতে পারে না। এ সময়কালের মধ্যেই তো এ বনের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সরকারের গভীর চিন্তা করা উচিত।
বন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে কী ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করেন?
বিদ্যুৎকেন্দ্রের পানি যখন ফেলা হবে, তাকে শতভাগ ঠাণ্ডা করার তো কোনো প্রক্রিয়া নেই। ফলে সুন্দরবনের পানির তাপমাত্রা বাড়বে। তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি বাড়লেও এই গরম পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খালি চোখে দেখা যায় না এমন যেসব অণুকণা পানিতে আছে, যেগুলো মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়ার খাবার, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। অণুকণাকে বলা হয় সব প্রাণীর জীবন। এখনো সময় আছে, এর মধ্যে নিরপেক্ষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে এসব পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
শ্রুতলিখন : ইব্রাহিম খলিল, রেনেসাঁ রহমান, তন্ময় রায় ও জাহিদ মিল্টন
[ ২ জুলাই ২০১৬, ঢাকা ]